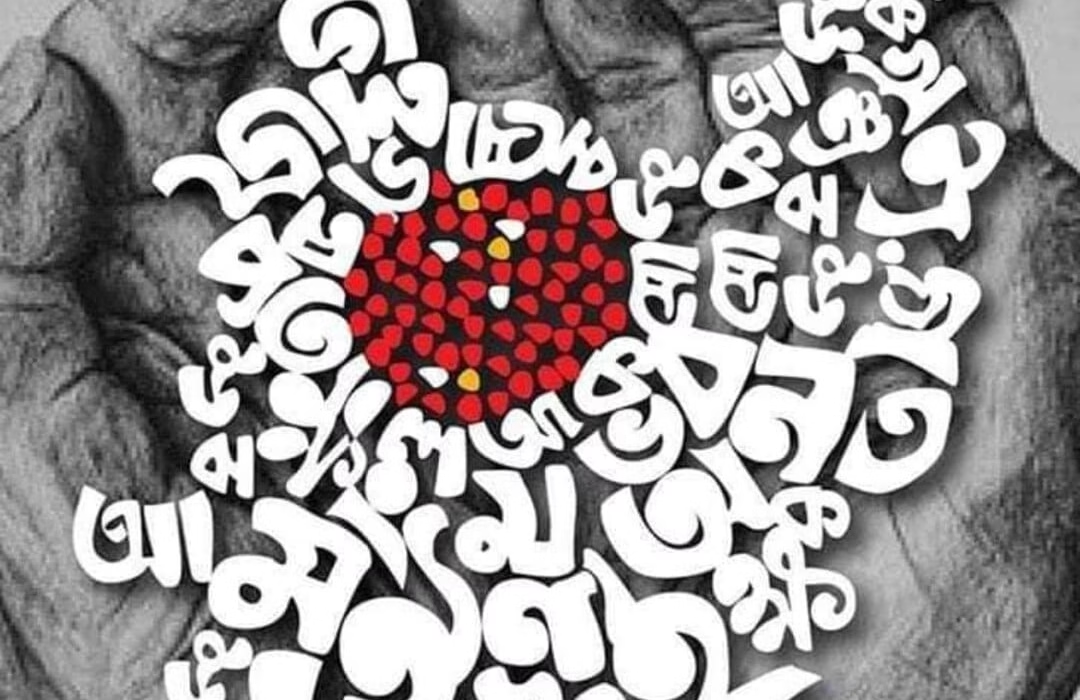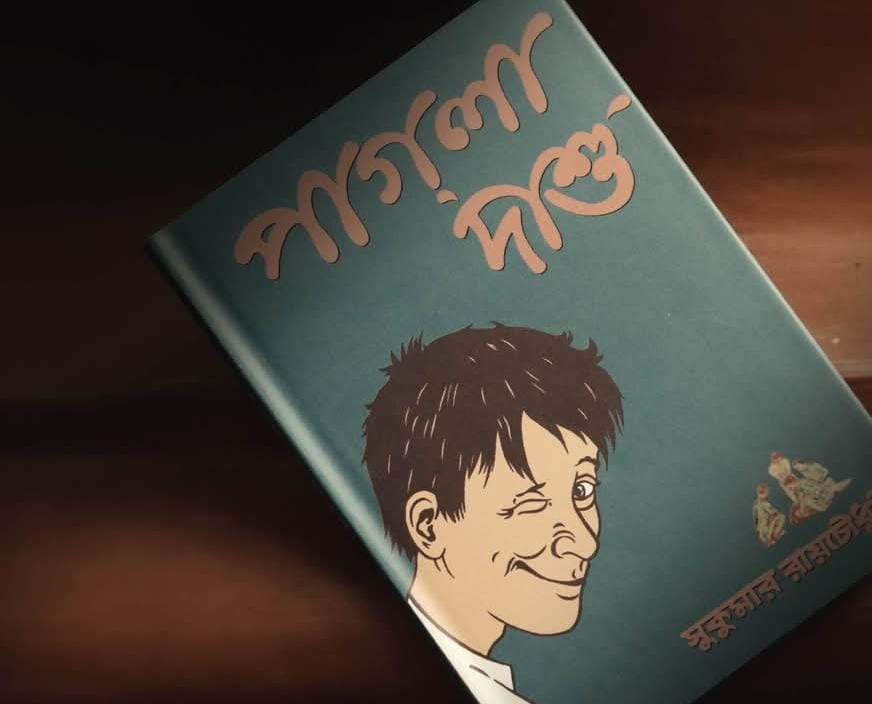আশ্বিনে বাজে আলোর মঞ্জীর, রব ওঠে জয় মা দুগ্গা। ঋতুমালার নিয়মমাফিক চলাচলে তারপর একদিন ফাল্গুনও আসে। তখন আবার জয় মা বাংলা ধ্বনিতে নীলাকাশ কাঁপে। জনমদুখিনী ভাষামাতৃকার ম্লানিমা দূরীকরণে পথে নামে তাঁর লাখো সন্তান। প্রভাতফেরিতে, টিভি নাট্যে, রেডিও অনুষ্ঠানে, ফেসবুক গ্রুপে দিনআখেরি হয়। একটা গোটা দিন, তার আগে- পরে কিছুটা সময় ভাষাটার জন্য আমরা যুদ্ধ করি, মূলত ফেসবুকে। তারপর আমরা চলে যাই নতুন একটা ভ্রমে, আনন্দে, আরেকটু বেশি উদ্দীপনার খোঁজে। কিন্তু এই যে একদিনের কলরব, ভাষার দুঃখ কি তাতে ঘোচে? ভাষা কেন দুঃখী হয়, যোদ্ধারা কি দু’দণ্ড সময় নিয়ে অন্য ঋতুতেও তা ভাবেন? নাকি হা-হুতাশটাও এক ধরনের উদযাপন, অভ্যেস, কিঞ্চিত সামাজিক সাংস্কৃতিক দায়? ভাবি ফি বছর।
আমাদের মনের চলন যেমন, রোদ এসে পড়লে, ছায়াময় রোয়াকে কেউ এসে বসলে তার ভালো লাগে, পরশে পরশে প্রাঞ্জল হয়ে ওঠে সে, যে কোনও ভাষারও তেমন একটা মনের গতি আছে। সে শ্বাসপ্রশ্বাস চায়, নানা আছিলায় বহতা নদীর মতো পথ বদলে এগিয়ে যেতে চায়। এই অভীপ্সার পূর্ণতা মানে ভাষার ক্রমবিকাশের পথ তৈরি হওয়া। একটা ঝকঝকে স্বাস্থ্যবান ভাষা থাকবে হাটেমাঠে, থাকবে হৃদয়ে, ঢুকে যাবে সরকারি অফিসে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে, মুদি দোকানের খাতায়, ছুটির আবেদনে, প্রেমপত্র থেকে শুষ্ক বিবৃতিতে। সমস্ত ভাঙচুর, নির্মাণ বিনির্মাণ সে বুকে ধারণ করবে, সমস্ত বৈপরিত্য তার অলংকার হবে, বলায় লেখায়, স্কুল কলেজ আদালত, ট্রেন-বাস সর্বত্র অপরিহার্যতা বজায় থাকবে তার। ভাষার সুস্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামাবে সরকারি সংস্থা। বিষে নীল ফুল ফোটাবে লিটল প্রেস, রোজ জল সার দেবে দৈনিক সংবাদপত্র, ছায়া দেবেন ভাষাসাহিত্যের বনস্পতিরা। নিরবিচ্ছিন এই নানামাত্রিক সাংঘর্ষিক প্রক্রিয়া জারি থাকলে তবেই ভাষা হবে অনন্তযৌবনা। দেশকাল ভেদে এই নিয়মটা এক। ভাষানদীর অসংখ্য শাখাপ্রশাখা থাকবে, মূলস্রোতই বাঁচাবে সেই নানাস্রোতকে। এমনটাই হয়েছে স্প্যানিশের ক্ষেত্রে। একুশটি দেশের আনুষ্ঠানিক ভাষা স্প্যানিশ। দেশভেদে সেই ভাষার বোল আলাদা, যেমন মেক্সিকোর অধিবাসীরা যে স্প্যানিশ বলেন, প্লাতা নদীর ধারের বাসিন্দাদের ভাষাটা তার চেয়ে ঢের আলাদা। শুধু স্পেনেই পাঁচ রকমের স্প্যানিশ বলা হয়। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কাস্তালান বলেন। কেউ কেউ বলেন কাতালান, হাতেগোনা লোক বলেন বাস্কে, গালিসিয়ান, আরানিস। দেখা যাচ্ছে, ভাষার আঞ্চলিক ভিন্নতা যেমন সযত্নে সংরক্ষিত তেমন আবার তা বহুস্রোতাও। মনে রাখতে হবে, কাস্তালান বলুন বা কাতালান, একজন স্পেনীয়র জন্য ভাষাটা তার হীনমন্যতা নয়, আত্মগরিমার অংশ। এপার বাংলায় আমরা সারা বছর কি এই গরিমায় গা ভাসাতে পারি? ভাষাকে দুখিনী বলার মধ্যে রোম্যান্স আছে, কোনো রোয়াব নেই।
একদম বুনিয়াদি স্তরে চোখ রাখি। সন্তানকে পড়ানোর জন্য অর্থের জোগান দিতে সক্ষম, এমন ক’জন বাবা মা আজ ছেলেমেয়েকে বাংলা মাধ্যমের স্কুলে পাঠান? পাঠান না কারণ এই ভাষাটা শিখে ঠোঁটস্থ করে কাজের জগতে খুব একটা সুবিধে পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ জনমদুখিনী ভাষা আজও কর্মদায়িনী নয়। যে স্কুলে এক ছাত্র অন্তত পাঁচ ঘণ্টা ভাষাটা অভ্যাস করতে পারে, তা আজ ক্ষয়িষ্ণু পরিবারগুলির অপারগতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সদরে মফসসলে। কলকাতার ক’টা স্কুলে ছাত্রদের বাংলায় প্রার্থনা গাইতে হয়? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, বাংলায় গান দূরের কথা, বহু স্কুলে শিক্ষকদের অলিখিত হুমকি দেওয়া আছে, স্কুলে বাংলা বলা যাবে না। সন্তানকে যার ছোঁয়াচ থেকে দূরে রাখতে চাই, তার জন্যে যুদ্ধ কীসের?
শিশুর পৃথিবী ছেড়ে আরেকটু এগনো যাক। বাংলা দৈনিকে অহরহ যে বিজ্ঞাপন ছাপা হয় তা প্রমাদে ছয়লাপ হয়ে থাকে। সংবাদমাধ্যমের দায় নেই, তারা জায়গাটা বিক্রি করে, কিন্তু বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলির কাজ এমন দায়সারা কেন? বাংলায় বিজ্ঞাপনের কপি লেখার যোগ্য লোক নেই। অথবা যোগ্য লোক থাকলে তাকে রাখার সামর্থ্য, অভিরুচি সংস্থাগুলির নেই। এসব কাজ বহু জায়গায় গুগল ট্রান্সলেটর সারে আজকাল। অথচ এই বাংলা ভাষাই উনিশ এবং বিশ শতক জুড়ে সংবাদমাধ্যমের বিজ্ঞাপনী অংশে কত না মণিমুক্তো ফলিয়েছে। আমরা অতীতের গৌরব হারালাম, নিঃশব্দে ভাষাটার মন মরে গেল, প্রতিদিনের এই আলো হাওয়ার স্পন্দন থেমে গেল, কেউ প্রতিবাদ করল না। কেউ জোরালো গলায় প্রশ্ন তুলল না রেডিও অনুষ্ঠানে ঘোষক কথায় কথায় ‘কেন কী’ বলছে কেন?
কাজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, আমাদের রাজ্যে অন্যান্য রাজ্যের মতোই তথ্য বাস্তুতন্ত্রের অনেকটা দখল করে বসেছে ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম। বাংলা ভাষায় লেখার মাধ্যমে আয় হয় সেখানে। অথচ অধিকাংশ ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম নিয়মিত লেখার জন্য বাংলা ফন্ট কেনে না। কাজ চালায় পাইরেটেড ফন্টে, যা ভেঙে যায়, জুড়ে যায়, ভাষার প্রতি আমাদের দায় ঠিক কতটা তা বোঝা যাবে এই ধরনের ভাঙা-জোড়া ডিজিটাল প্রতিবেদন পড়লেই। ভাষাকে ব্যবহারিক করে তুলতে মূল্য দিতে প্রস্তুত নয় কেউ।
ইংরেজি দৈনিকের সমস্তটার মতো বিজ্ঞাপনও প্রায় নির্ভুল। কারণ এই ভাষায় কপি সম্পাদনা করে ছেলেমেয়ে অন্ন সংস্থান করতে পারবে এই বিশ্বাস বাবা-মায়ের আছে, তাই কপি লেখা শিখে কাজে এসেছে অনেকে। ইংরেজি ভাষা বাবা-মায়ের মধ্যে এই আস্থা সঞ্চার করতে পেরেছে। বাংলা ভাষা পারেনি। বাবা মা চান না শিশু বাংলা বলা লেখায় ততটা দক্ষ হয়ে উঠুক, প্রুফ রিডার বা কপি এডিটর হোক। একটি দু’টি আবৃত্তিযোগ্য কবিতা জানলে ভালো, তাতে প্রতিবেশীর ছানার তুলনায় নিজের ছানাকে উন্নততর ব্র্যান্ড হিসেবে প্রমাণ করা যায়। কিন্তু এটুকুই। ভাষার দক্ষতা ভাত দেবে না নিশ্চিত। যে ভাষা রুজি দেয় না, তার জন্যে অশ্রুমতী রাজকন্যে সেজে মনখারাপ করা যায়, অতীতচারণায় মগ্ন হওয়া যায়, কিন্তু দিনানুদিন অহংকার করা যায় না। বুক বাজিয়ে বলা যায় না, বাংলা ছাড়া আর কিছু বলি না ভাই। এই শহরে বসেই ক্রেডিট কার্ড গছানোর জন্যে দিনে তিনবার ফোন করে সুমিষ্ট গলার হিন্দিভাষী। আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আমরা তাকে বলতে পারি না, বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বলি না। প্রশ্ন করি না, উত্তরপ্রদেশে বাংলায় ক্রেডিট কার্ড বিক্রি করা যায় কিনা। ম্যান্ডারিন চাইনিজ বা স্পেনীয়রা কিন্তু এখানেই শাহমাত করেছে। পরাভবের মুখে নুন দিয়ে বেঁচে আছে সহস্রধারার এই ভাষাদুটি। আর আমরা, কোটি কোটি লোকের মুখের ভাষাটাকে কল সেন্টারের ভাষা হিসেবেও দাঁড় করাতে পারলাম না আত্মবিশ্বাসের অভাবে। অর্থনৈতিক ভাবে বাংলা প্রকৃতই রুগ্ন, ক্ষয়াটে, জনমদুখিনী, অক্ষমের ভাষা।
‘প্রভু’ চলে গিয়েছে, যাওয়ার বেলায় মেরুদণ্ডটাও চেয়ে নিয়ে গিয়েছে, সেই থেকে যে ন্যুব্জ হয়ে আছি, মণীষার আলো আসে-যায়, আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পারি না। ভাষাটাকে একটা আর্থিক কাঠামো দিতে কোমর বেঁধে নামতে পারি না। এমনকী একটা বানান সাম্যেও পৌঁছতে পারি না। প্রতিদিনের লব্জবদল ঠাওর করে নতুন পরিভাষা কোষ তৈরি হয় না কিছুতেই। এই কাজটি যাদের করার, তারা জেনে না জেনে, আলস্যে বা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় দায়িত্ব থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেন।
কেউ বলতেই পারেন, এই তো বইমেলা গেল, কয়েক কোটি টাকার বই বিক্রি হলো। ভাষা তো বহাল তবিয়তে আছে, এত মরাকান্না কীসের! এখানেই দরকার ছানবিন, যাচাই। যে পরিমাণ বাংলা বই বিক্রি হয়েছে, এর মধ্যে ঠিক কত বইয়ের গঠন আন্তর্জাতিক মানের? কত বইয়ের প্রুফরিডিং নিখুঁত? কত বইয়ের ছাপাই, বাঁধাই ভালো? সমীক্ষা চালালে দেখা যাবে সংখ্যাটা দশ শতাংশের বেশি নয়। এমনকী বহু নামকরা প্রতিষ্ঠানও দায়সারা কাজ করেছে, সময়ে কাজ শেষ করতে পারেনি। আসলে ছাপাখানা ও তদসংক্রান্ত কাজগুলির সঙ্গে জড়িত মানুষের মধ্যে অধিকাংশই খুব অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করেন বছরের পর বছর। কোনোরকমে ভাত জুটিয়ে নেন, উন্নতির তাগিদ বা সুযোগ কোনোটাই থাকে না তার। সংগঠিত অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো নির্দিষ্ট সময় পর চাকরিবদলের সুযোগ বড় একটা থাকে না। চাপ নেওয়া, সঠিক সময়ে কাজ দেওয়ার মতো পেশাদার মনটা গড়েই ওঠে না। যে টাকা একজন প্রুফরিডার পাচ্ছেন তাতে তার পক্ষে দারিদ্ররেখা অতিক্রম করা সম্ভব না। তিনি কেন উৎকর্ষের দিকে ঝুঁকবেন! সমস্ত না-এই সম্মিলিত ভাবে প্রতিফলিত হয় বইমেলায়। অথচ প্রত্যেক প্রকাশকের কাছে একজন কপি এডিটর, একজন দক্ষ প্রুফরিডার, দক্ষ ছাপাই বাঁধাইয়ের লোক থাকলে ছবিটা বদলে যেত। এমনটা হয় না, রাজত্ব করে খুঁত, কারণ নিখুঁত বই কারিগরি জানা একজন যুবা যদি দক্ষতার মাপকাঠি অনুযায়ী পারিশ্রমিক চায়, অধিকাংশ প্রকাশক তাকে তা দিতে পারবে না। টানাটানির সংসার। মেলামাঠে দেদার বিক্রি হচ্ছে থ্রিলার, তন্ত্রের কুৎসিত প্রচ্ছদের বই। ওয়েব সিরিজের ক্ষেত্রেও তো এগুলিরই কাটতি বেশি। এগুলি কেউ ভাষাকে ভালবেসে পড়ে না, দেখে না, নিছকই অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের তাড়নায় এ পথে গমন উন্মত্ত জনতার। ভাষাপ্রেম, বইপড়া, নিবিড় পাঠের সঙ্গে এই ক্রয়ের জোরালো কোনো সম্পর্কই নেই।
আমাদের উৎসবের আলোটা ফিকে হলেই দেখি, জেলার ছেলে শহরে এসে তার বাকভঙ্গিমার জন্য উপহাসের পাত্র হচ্ছে আজও। কাগজে প্রতিবেদন পড়ি, বাংলাটুকু জানার এবং ইংরেজি না জানার হীনমন্যতা নিয়ে কুলীন কলেজ ছাড়ছে জেলার পড়ুয়ারা। খুব অল্প লোকের দালানে ভাষার যে সলতেটুকু আজও জ্বলছে তাকে ক্ষমতায়নের জন্য ব্যবহার না করে ক্ষমতার ভাষায় পরিণত করতে পেরেছি আমরা। তাই একটা দিনের ছায়াযুদ্ধ পার করে দিতে পারলেই ফেসবুকের দখল নেয় মুরাদ টাকলা। রোমান হরফে ভাষাতর্পণ। আর জনমদুখিনী ভাষা, ওই যে ছেলে বাংলাটুকু জানে বলেই বড় কলেজের গেট থেকে মাথা হেঁট করে বেরোলো, তার পাশাপাশি হাঁটছে, বড়রাস্তা, হাইওয়ে পেরিয়ে, আলপথের ধারে তখন নিঝুম সন্ধে। ভাষা আমার হারিয়ে যাবে মরা আঁধারে।