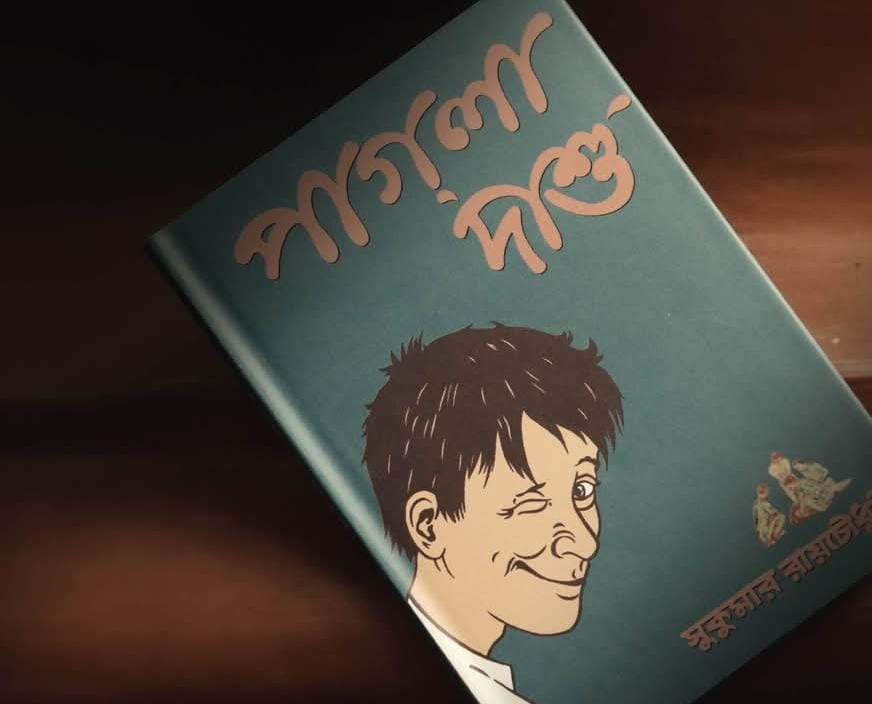এবার একটা এসপার-ওসপার হবে। নজরুল ইসলাম অবমাননার বদলা নেবে বাঙালি। ফেসবুকে বাঙালির মেজাজ, বাদানুবাদ দেখে এমনটাই মনে হচ্ছে। এমন গভীর নিবেদন, অনুরাগ তো একদিনে তৈরি হয় না। দীর্ঘদিনের ভালো-লাগা, সযত্নলালন না থাকলে কেউ এ হেন অধিকার প্রদর্শন করবে কী করে! রহমানের ভুল নিয়ে আর পাঁচজনের মতোই ক্রুদ্ধ, ব্যথিত আমি নজরুলের প্রতি কলকাত্তাইয়া তথা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালির যত্নের আড়বহরের দিকে তাকাই।
দাঁড়িয়ে আছি তালতলা লেনে। এই রাস্তারই এক প্রান্তে রয়েছে সেই ঐতিহাসিক বা়ড়ি। যেখানে বসে বিদ্রোহী কবিতাটি লিখেছিলেন নজরুল ইসলাম। বাড়িটির বর্ণনা পাওয়া যায় মুজফফর আহমেদের লেখায়। মুজফফর লিখছেন, “আমাদের ৩/৪সি, তালতলা লেনের বাড়িটি ছিল চারখানা ঘরের একটি পুরো দোতলা বাড়ি। তার দোতলার দু’খানা ঘর ও নীচের তলার দু’খানা ঘর ছিল।…বাড়ির নীচেকার দক্ষিণ পূর্ব কোণের ঘরটি নিয়ে থাকি। এই ঘরেই কাজী নজরুল ইসলাম তার বিদ্রোহী কবিতাটি লিখেছিলেন।” এই বিদ্রোহী কবিতাই নজরুলের আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। মুজফফর আহমেদ লেখেন, “বৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও কাগজের চাহিদা এত বেশি হয়েছিল যে, শুনেছিলাম সেই সপ্তাহের কাগজ দু’বার ছাপা হয়েছিল।” সব মিলে ২৯ হাজার কাগজ ছাপা হয়। মুজফফরের ধারণা অনুযায়ী, ২ লক্ষ লোক কবিতাটি পড়েছিলেন। ঝিমিয়ে আসা বিপ্লববাদকে যেন নতুন করে ঝাঁকুনি দিয়েছিল এই কবিতা। এ হেন শিল্পের স্মৃতিজাগানিয়া বাড়িটি নিশ্চয়ই দেখার মতোই হবে! প্রত্যাশা নিয়ে গিয়ে যা জানলাম, জনৈক সীমা সাহা এই বাড়িটি আগের মালিকপক্ষের থেকে কিনে নিয়েছেন। বাড়ির প্রবেশদ্বারের গায়ে সাদা টাইলস বসানো দেওয়ালে, একদম কেন্দ্রে বসানো নামফলকে বড় বড় করে লেখা- ‘মা বিপদনাশীনির কুঠীর।’ সীমা সাহা জানালেন, নজরুল ইসলাম এ বাড়িতে থাকতেন তিনি জানেন। কিন্তু যেহেতু কবিতায় তাঁর ‘ইন্টারেস্ট’ নেই তাই বিদ্রোহী কবিতাটি তিনি পড়েননি। মুজফফরের লেখায় পড়া দক্ষিণ-পূর্বের ঘরটি দেখতে চাইলাম। সীমা সাহা নিয়ে গেলেন সেই ঘরে। একগাল হেসে বললেন, ‘নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছি।’ দেখলাম, লম্বা ঘর, মেঝে মোজাইক, সারাঘর সাদা টাইলসে মোড়া, কটকটে নীল দুটো সোফা রাখা। জিজ্ঞেস করলাম, কেউ অতীতে এই বাড়িতে এসেছেন? চোখ টিপে বললেন, ‘কেউ না। কেউ কেউ রাস্তার মুখে ফলকটা দেখে চলে যায়। ভাবে ফলক লাগোয়া বাড়িটাই বুঝি ওই বাড়ি।’ এ আর রহমান নজরুল ইতিহাস বিকৃত করেছে বলে অভিযোগ যাদের, তারা কি এই গোটা ঘটনাকে ইতিহাস বিকৃতি হিসেবে দেখেন? এই ইতিহাস রক্ষার দায় কার ছিল? মনে পড়ে, নিজে গিয়ে দেখে এসেছি এর চেয়েও খারাপ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত আরও একটি বাড়ি, ঠিকানা ৭, প্রতাপ চ্যাটার্জী লেন। যেখানে নজরুল থেকেছেন, আবার ধূমকেতু পত্রিকার কাজকর্মও চলেছে। এই অনাদর, অবহেলা কি স্রেফ নজরুলের জন্যেই বরাদ্দ? বোধহয় নয়। জীবনানন্দ দাশ, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন কলেজ স্ট্রিট লাগোয়া প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে। তার একটা অংশে জমজমাট পাইস হোটেল। অন্য অংশে, দুই মহৎ লেখাজীবীর ধুলোমলিন ঘর। সেখানে চাঙর খসে পড়ছে যত্রতত্র। বাঁশ দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে কড়িবর্গা। পাইস হোটেলের খদ্দেররা জানেনও না এই ইতিহাসের কথা। কারো কোনো দায় নেই। প্রশ্ন হলো, মিডিয়ায়-সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা এ আর রহমানের শাস্তি দাবি করছেন, তারা এক্ষেত্রে কার মুণ্ডপাত করবেন? আয়নায় নিজের মুখ দেখে আমাদের সংস্কৃতিপ্রেমী সমাজ?
তার্কিক বলতে পারেন, ইট কাঠ কংক্রিটের দেওয়ালে কি একজন শিল্পীকে খোঁজা যায়! তিনি তো আছেন ছাপার অক্ষরে। গবেষকের অনুসন্ধানে। এ কথা মেনে নিয়েই চোখ রাখি ইতিহাসে। খুঁজে দেখত চাই, নজরুল সংরক্ষণের বিষয়ে আমরা কতটা সচেতনতা দেখিয়েছি।
১৯২০-১৯৩০ সালের মধ্যে সাংবাদিকতার জগতে ঝড় তুলেছেন নজরুল ইসলাম। নবযুগ, ধূমকেতু, লাঙল, গণবাণী, নবপর্যায়ের নবযুগ—এই পাঁচটি জায়গায় নজরুল সম্পাদক হিসেবে বিশেষ শাখায় তাঁর পারদর্শিতার চিহ্ন রেখেছেন। এছাড়াও লিখেছেন সওগাত-সহ নানা ছোট পত্রিকায়। কিন্তু জীতেন্দ্রনাথ বসু, মোহিত মৈত্র, জে নটরাজন, মোহিত মৈত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ– মান্য ইতিহাসবিদরা সকলেই নিজেদের লেখায় সচেতন ভাবে তাঁর নাম বাদ দিয়ে গিয়েছেন। যা নিয়ে এত বিতর্ক, সেই ‘ভাঙার গান’ নামেই নজরুলের কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে, অর্থাৎ ১৯২৪ সালের অগাস্ট মাসে। বইয়ের প্রথম লেখা কারার এই লৌহ-কবাট। সব মিলে এগারোটি স্বতন্ত্র লেখা ছিল এই গ্রন্থে, যার অধিকাংশই আগে ধূমকেতুতে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে সংকলতি একটি পদ্য- ‘সুপার (জেলের) বন্দনা’ রবীন্দ্রনাথের তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে-র প্যারোডি। এই পদ্যের পাদটীকায় বলা আছে, ‘হুগলি জেলে থাকাকালীন জেলের সকল প্রকার জুলুম আমাদের ওপর দিয়ে পরখ ক’রে নেওয়া হয়েছিল। সেই সময় জেলের মূর্ত্তিমান ‘জুলুম’ বড়-কর্তাকে দেখে এই গান গেয়ে আমরা অভিনন্দন কর্তাম।’ উল্লেখ্য, ১৯২৩ সালের ১৪ই এপ্রিল তাঁকে পাঠানো হয়েছিল হুগলি জেলে। জেল কর্তৃপক্ষের অকথ্য অত্যাচারে পরের দিন থেকেই নজরুল অনশন শুরু করেন। অর্থাৎ ধরে নেওয়া যাচ্ছে এই গানটি অনশনরত অবস্থায় কবি লিখছেন, গাইছেন। কারার ওই লৌহকবাটের হোক বা এই প্যারোডি, সব মিলিয়ে এমন ঐতিহ্যবাহী, ঐতিহাসিক গ্রন্থ তো ঘরে ঘরে থাকা উচিত। ধ্রুপদী বইয়ের মর্যাদা দিয়ে তার বিশেষ বিপণন কাম্য। ইতিহাসসচেতন মানুষ স্মারক হিসেবে এই বই ঘরে রাখবে, কালেক্টরস এডিশন দাবি করবে-এমনটা আশা করা যায় না কি! কিন্তু কলকাতা শহরের উল্লেখযোগ্য সমস্ত বাংলা বইয়ের দোকানে যোগাযোগ করে বইটির হদিশ পাওয়া গেল না। দে বুক স্টোরের কর্ণধার দীপু দে বিরক্ত মুখেই বললেন, ‘নজরুলের বইয়ের আগের মতো বিক্রি নেই। কেউ কেউ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যেই রচনাবলী চায়। কিন্তু দিতে পারি না। কারণ নিয়ম হলো ১০০ বই তুলতে হবে। এদিকে সরকার প্রকাশিত কোনো রচনাবলীই পুরো সেট পাওয়া যায় না। কেউ ইনভেস্ট করলে তো পুরো বইটা এক সঙ্গে চাইবে। তা যদি না পাওয়া যায়, কোন সাহসে কোনো দোকানদার ১০০ বই তুলবে!’
ভাঙার গান গ্রন্থটির কোনো আন্তর্জাতিক অনুবাদ নেই। নজরুলের জীবন ও কাজ নিয়ে এ যাবৎ কালে ব্লুমসবেরি বা অক্সফোর্ডের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা দুই। সেই গ্রন্থদু’টির খোঁজ নিলাম কলকাতার অক্সফোর্ড, স্টোরি, বাহরিসনসের মতো নামী গ্রন্থবিপণিতে। জানানো হলো, ‘নট অ্যাভেলবল নাউ’। চাইলে অবশ্য আনিয়ে দেওয়া যেতে পারে। অগ্রিম টাকা দিতে হবে। দশদিন সময় লাগবে। অর্থাৎ বোঝা যায়- দশটি জেন উপদেশ, সদগুরুর বাণীর যা চাহিদা, নজরুলের গ্রন্থের সেই চাহিদা নেই। সেই কারণেই গা করে না বিপণীগুলি।
হতাশ মনে কাগজ পড়ি, বাঙালির নজরুল বাঁচাও যুদ্ধ দেখি সোশ্যাল মিডিয়ায়। দেখি, সমাজমান্য গবেষক জানান দিয়েছেন, কারার এই লৌহকবাট কবিতাটি নজরুল ইসলাম চিত্তরঞ্জন দাশের ছেলের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এমনটা নাকি লিখেছেন মুজফফর আহমেদ। নজরুল ইসলামের কামরাদারির বন্ধু মুজফফর আহমেদ লেখায় চোখ রাখি। দেখি তিনি লিখেছেন, “১৯২১ সালে ১০ ডিসেম্বর তারিখে চিত্তরঞ্জন গিরেফতার হয়ে জেলে গেলেন। তারপর তাঁর স্ত্রী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী ”বাঙ্গলার কথা”-র সম্পাদিকা হলেন। এই সময়ে তিনি একদিন দাশ পরিবারের তার দেবর সম্পর্কিত শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশকে ”বাঙ্গলার কথা”য় ছাপানোর উদ্দেশ্যে একটি কবিতার জন্যে নজরুল ইসলামের নিকটে পাঠালেন।” দেবর বা দেওর শব্দের অর্থ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চিত্তরঞ্জনের পুত্রসন্তানের নাম চিররঞ্জন।
ভ্রান্তিবিলাস আমাদের অধিকার। তথ্যবিকৃতি আমাদের মুদ্রাদোষ। যত্নে, মনোযোগে আমাদের আলস্য। কিন্তু দোষ শুধু এ আর রহমানের। রহমানকে বরং ধন্যবাদ, তিনি বাঙালির মনস্তত্ত্ব উন্মোচনের একটা সুযোগ তৈরি করেছেন। আমাদের স্থূলেই ভুল। আমাদের খালি দায় ঝেড়ে ফেলা। আমাদের স্রেফ মূর্তিতে মাল্যদান। নিজেদের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে কবি সেই কবেই বলেছেন, “সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী, রেখেছ বাঙালী ক’রে, মানুষ করোনি।”